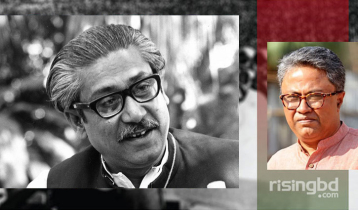আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎসব

আমাদের ছেলেবেলায় ঝিনুকের খোলকে পাথরে ঘষে ঘষে ফুটো করে কাঁচা আম ছিলে খেতাম। তবে একটা রীতি ছিল, পরবের আগে আম খাওয়া যাবে না। পরব মানে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন- পহেলা বৈশাখ। ফেনী অঞ্চলের মানুষজনের উচ্চারণে ‘প’ বর্ণটি যে অজ্ঞাত কারণে ‘হ’ হয়ে যায়, একথা মোটামুটি সবার জানা। যেমন তারা পানিকে বলে হানি, শালাকে হালা, ফেনীকে হেনী। সেই হিসেবে পরবকে বলে হরব। পরব বা হরবের আগে কেন আম খাওয়া যাবে না? কারণ, পরবের আগে শক্ত হয় না আমের আঁটি। অর্থাৎ আম প্রাপ্তবয়স্ক হয় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক আম খাওয়া যাবে না। ছেলেবেলায় আম খাওয়ার জন্য আমরা পরবের অপেক্ষায় থাকতাম। পরবের দিনে লবণ-মরিচ দিয়ে বানিয়ে আম খাওয়ার ধুম লেগে যেত। এটাই ছিল আমাদের ছেলেবেলার পহেলা বৈশাখের প্রধান উৎসব।
আরেকটি উৎসব ছিল চৈত্রসংক্রান্তির দিন। এ দিন আমাদের গ্রামে আসত দশ-বারোজনের একটি যাত্রাদল। আমরা বলতাম ‘ডাই’। ডাই মানে কী জানতাম না। পরবর্তীকালে অভিধান ঘেঁটে এমন কোনো শব্দ পাই নি। পেয়েছি ‘ঢাকি’। ঢাকি মানে যে ব্যক্তি ঢাক বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ধারণা করি, আঞ্চলিক ভাষায় পানি যেমন হানি হয়ে যায়, ঢাকিও তেমনি ডাকি হয়ে গেছে। মানুষ ডাকিকেও জায়গামতো রাখে নি, করে দিয়েছে ডাই।
চৈত্রসংক্রান্তির দিন হতো চড়কপূজা। আমাদের বাউরখুমা গ্রামের দু’দিকেই ত্রিপুরা সীমান্ত। উত্তর সীমান্তে, অর্থাৎ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমা শহরের দক্ষিণের মাঠে, নো-ম্যান্স ল্যান্ডে, প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হতো। এখনো হয়। বাবা-মায়ের বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে সবান্ধব চলে যেতাম চড়কপূজা দেখতে। এপার-ওপারের হাজার হাজার মানুষ সমবেত হতো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। শেষবিকেলে ঘুরানো হতো চড়কগাছ। দুজন সন্ন্যাসী পিঠে দড়ি বেঁধে চড়ে বসতো চড়কগাছে। চক্রাকারে ঘুরতো চড়ক, চড়কের সঙ্গে ঘুরত সন্ন্যাসী। সেই বয়সে এর চেয়ে বড় বিস্ময় আমাদের কাছে আর কিছু ছিল না। চড়কে ঘুরতে ঘুরতে সন্ন্যাসী তার হাতে ধরা ঝুড়ি থেকে ছিটাতো নকুলদানা আর বাতাসা। ছিটানো হতো নিচ থেকেও। সেসব কুড়ানোর জন্য শুরু হতো মানুষের হুড়োহুড়ি। কতই না মজার ছিল সেসব খাবার! অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আমরা চলে যেতাম ওপারে। বিডিআর বা বিএসএফ বাধা দিতো না। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হতো চড়কপূজা। সবাই ফিরে যেতো নিজ নিজ বাড়ি। মন খারাপ করে আমরাও হাঁটা ধরতাম বাড়ির দিকে।
পরদিন পহেলা বৈশাখ। এদিন সবাই মিলে আম খাওয়া ছাড়া উদযাপন করার মতো আমাদের কোনো উৎসব ছিল না। গ্রামের দোকানদারেরা দোকানের সামনে কলাগাছ পুঁতে এবং রঙিন কাগজ দিয়ে দোকানগুলো সাজাতো। অনুষ্ঠিত হতো বার্ষিক পুণ্যাহ বা হালখাতা। এগুলো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। পরবর্তীকালে লেখালেখির প্রয়োজনে চৈত্রসংক্রান্তি ও বৈশাখকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান করে অনেক কিছু জানতে পারি। জেনেছি, চড়কপূজা হচ্ছে চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব। গাজন উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ চড়কপূজা। এ উৎসব উপলক্ষে এক গ্রামের শিবতলা থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে অন্য শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন শিব ও একজন গৌরী সেজে নৃত্য করে এবং অন্য ভক্তরা নন্দি, ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতি সেজে শিব-গৌরীর সঙ্গে নাচে। এসময় শিব সম্পর্কে নানারকম লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হয়, যাতে শিবের নিদ্রাভঙ্গ থেকে শুরু করে তার বিয়ে, কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে। শিবপূজা উপলক্ষে মেলাও বসে। অতীতে এসব মেলায় ভক্তদের শূলফোঁড়া, বানফোঁড়া ও বড়শিগাঁথা অবস্থায় চড়কগাছে ঘোরানো, কাঁটা জাতীয় গাছের শাখা-লতা কিংবা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি সব ভয়ংকর ও কষ্টসাধ্য শারীরিক কসরত দেখানো হতো। সূর্য পাটে গেলে পিঠে বড়শি বিঁধিয়ে, গলায় সাপ পেঁচিয়ে চড়কগাছে উপুড় হয়ে ঘুরত সন্ন্যাসী। পিঠে বড়শি বিঁধানোর এই রীতি এখন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে কোনো কোনো অঞ্চলে গীত হয় অষ্টক গান। পৌরাণিক কাহিনিকে সুরে বেঁধে সাত-আটজন মিলে এই ধারার গান গায়। ‘হর-পার্বতী সংবাদ’, ‘পার্বতীর বিলাপ’, ‘শিবের বিয়ে’ প্রভৃতি পালাগান গায় তারা। দেলপূজা বা চড়কপূজার স্থানেই সাধারণত অষ্টক গানের আসর বসে। এ ধারার গান গাওয়ার উদ্দেশ্য মূলত দেবাদিদেব শিবকে সন্তুষ্ট করা। বাড়ি বাড়ি গিয়েও অষ্টক গান শোনায় গায়করা। এতে ছেলেরা মেয়ের পোশাক পরে মেয়ে সাজে। তাদের গায়ে থাকে বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ পোশাক এবং মুখ থাকে নানা রঙে রাঙা। বিশেষত খুলনা অঞ্চলে এই গান গাওয়া হয়।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। জেলে, ঘোষ, চণ্ডাল, দাস ও তাঁতিরা এ দিন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে জাঁকজমকভাবে শিবপূজা করে। শিবভক্তরা দুর্গা, কালী ও নানা দেবদেবীর রূপ ধারণ করে বাড়ি বাড়ি মাগন করে। তখন তারা নাচে, গায় এবং বাজায় নানা বাদ্য। ২৬ চৈত্র থেকে এই মাগন শুরু হয়। সংক্রান্তিতে এসে আয়োজন করে চড়কপূজার। এদিন বিকেলে প্রতি পাড়া থেকে দশ-পনেরোজনের একেকটি দল বের হয়। রঙে রাঙানো থাকে তাদের মুখ, হাতে থাকে কাঠের তলোয়ার, মুখে থাকে রক্তজবা, কোমরে পেঁচানো থাকে এক টুকরো সালু কাপড়, আর মাথায় পাগড়ি। দলনেতার হাতে থাকে একটি মুণ্ডু। এটিকে স্থানীয়ভাবে ‘লাল কাছ’ বলা হয়।
দুইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানিকগঞ্জ জেলার বাগবানিয়াজুড়ি গ্রামের মাঝিপাড়ায় চৈত্রসংক্রান্তির উৎসব হয়ে আসছে। স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় এই উৎসবের আয়োজক। চৈত্র মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। ঢাকি ও নৃত্যকের দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান-বাজনা করে। তাদের সঙ্গে থাকে শিবের অর্ধশায়িত মূর্তি, যাকে বলা হয় ‘দেল’। কাঠ দিয়ে বানানো হয়। এর একদিকে থাকে ত্রিশূল। চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় দুর্গা, কালী, অসুর, বাঘ বা বানরের মুখোশ পরে গান-বাজনা ও নাচসহ পরিবেশিত হয় অসুরবধের পৌরাণিক কাহিনি। একে বলা হয় ‘মুখাকাজ’। মানিকগঞ্জের বিভিন্ন মন্দিরে চলে এই মুখাকাজ উৎসব।
গোপালগঞ্জে পাটবান পূজা হয় চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে। শিবভক্তরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পাটবান মাথায় করে গ্রামফেরিতে বা মাগনে বের হয়। মাগনের টাকা বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে করে পূজার আয়োজন। নিম বা বেলগাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয় পাটবান। দশ অবতার তথা গঙ্গা, ভীগরথ, বামন, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম, সর্প, পহ্লাদ, শঙ্খ ও পদ্মের মূর্তি আঁকা থাকে পাটবানে। সৌন্দর্য বাড়াতে এসব মূর্তির গায়ে দেয়া হয় তেল ও সিঁদুর। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার সিদ্ধার্থখোলা মন্দির, দিঘলিয়ার কালীবাড়ি মন্দির, পিনজুরির প্রশান্ত দের গোভিটায়, টুঙ্গিপাড়ার পরিমল সাহার বাড়ির মন্দির, গোপালগঞ্জ সদরের বালাবাড়ির মন্দির, কাশিয়ানীর সিঙ্গা গ্রামের জগৎপট্টির মাঠসহ অনেক স্থানে পাটবান পূজা অনুষ্ঠিত হয়।
গাজন একটি লোকউৎসব। চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে আষাঢ়ি পূর্ণিমা পর্যন্ত সংক্রান্তি বা পূর্ণিমা তিথিতে এ উৎসব উদযাপিত হয়। এ উৎসবের সঙ্গে জড়িত নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাদের নাম। যেমন শিবের গাজন, নীলের গাজন ইত্যাদি। উৎসবটির মূল লক্ষ্য সূর্য ও তার পত্নীরূপে কল্পিত পৃথিবীর বিয়ে দেয়া। গাজন উৎসবের পেছনে কৃষক সমাজের একটি সনাতনী বিশ্বাস কাজ করে। অপরদিকে, হিন্দু পঞ্জিকা মতে চৈত্রসংক্রান্তির দিনকে গণ্য করা হয় মহবিষুব সংক্রান্তি নামে। এদিনে হিন্দুরা পিতৃপুরুষের তর্পণ করে থাকে, নদীতে বা দিঘীতে পূণ্যস্নান করে থাকে। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পূণ্যজনক মনে করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক স্থানে, বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে, গম্ভীরাপূজা বা শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।
কোনো কোনো অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির রাতে রান্না করা ভাতে পানি দিয়ে পান্তা করে রেখে পরদিন পহেলা বৈশাখে নানা ধরনের মাছ ও ভর্তা সহকারে খাওয়া হয়। এছাড়া রয়েছে আমানি। এটি একটি প্রাচীন কৃষিভিত্তিক লোকাচার। বাড়ির কর্ত্রী আমগাছের কচি পাতার একটি ডগা রাতেরবেলায় একটি মাটির ঘটিতে ভিজিয়ে রাখেন এবং পহেলা বৈশাখ সকাল বেলা হালচাষে যাওয়ার সময় স্বামী বা ছেলের গায়ে সেই পানি ছিটিয়ে দেয়। এতে সারা বছরের জন্য কল্যাণ হবে বলে তাদের বিশ্বাস।
অপরদিকে, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে মেলা। ঢাকার বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত হয় লোকমেলা। সারা দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের সমারোহ ঘটে এই মেলায়। ঐতিহ্যবাহী ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনে প্রায় চারশ বছর ধরে বৈশাখী মেলা হয়ে আসছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ব্যতিক্রমী এক মেলা বসে, যার নাম ‘বউমেলা’। পাঁচ দিনব্যাপী চলে। সোনারগাঁ থানার পেরাব গ্রামের পাশে অনুষ্ঠিত হয় ঘোড়ামেলা। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে স্মৃতিস্তম্ভে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি করে মাটির ঘোড়া রাখে এবং এখানে মেলার আয়োজন করে। এ কারণে লোকমুখে প্রচলিত মেলাটির নাম ঘোড়ামেলা। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ নৌকায় খিঁচুড়ি রান্না করে রাখা এবং সবাই কলাপাতায় আনন্দের সঙ্গে খাওয়া।
পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী পালন করে বৈসাবী উৎসব। বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ থাকে তাদের এই আয়োজন। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে আলাদা প্রথা। খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর গরয়া নৃত্য। বর্ষবরণ উৎসবকে তারা বলে বৈসুক। রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত হয় মারমা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জলক্রীড়া বা জলোৎসব। বর্ষবরণ উৎসবকে মারমারা বলে ‘সাংগ্রাই’। উৎসব চলে তিন দিন ধরে। কাপ্তাইয়ের চিৎমরমে অনুষ্ঠিত হয় সবচাইতে বড় জলক্রীড়া। একটি বড় মাঠের মাঝখানে বাঁশ দিয়ে দুই ভাগ করা হয়। দুই পাশে বড় বড় জলের পাত্রে রাখা হয় জল। ছেলে ও মেয়েরা দুই দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পানি ছিটিয়ে উৎসবটি পালন করে। তাদের বিশ্বাস, এ উৎসবের মাধ্যমে বিগত বছরের পাপ-তাপ-গ্লানি ধুয়েমুছে যাবে। বাঙালিরাও দেখতে যায় উৎসবটি।
বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট কর্তৃক ঢাকার রমনা পার্কে বর্ষবরণ উৎসব এখন আমাদের ঐতিহ্য। ১৯৬৭ সালে রমনা পার্কের অশ্বত্থমূলে ছায়নট প্রথমবারের মতো বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছিল ২০০১ সালে। তখন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় অনেকে হতাহত হয় কিন্তু তারপর এই অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়ে নি।
বর্ষবরণ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজন করে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা অনুষ্ঠান। ছাত্র-শিক্ষক মিলে বের করে বিশাল মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা এখন ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায়।
বর্ষবরণের উৎসবকে বলা হয় অসাম্প্রদায়িক উৎসব। সত্য। বাংলাদেশে এই ধরনের বৃহৎ অসাম্প্রদায়িক উৎসব দ্বিতীয়টি নেই। প্রশ্ন করা যেতে পারে, উপরে চৈত্রসংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখকেন্দ্রিক যেসব আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেয়া হলো তার সবই তো পালন করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। তাহলে এই উৎসব অসাম্প্রদায়িক হলো কেমন করে? সবিনয় উত্তর, প্রশ্নটি সঠিক নয়। চৈত্রসংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে যেসব আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত, তার সবই একতরফাভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পালন করে না, মুসলমানরাও অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন বার্ষিক পুণ্যাহ বা হালখাতা উৎসব মুসলমান-হিন্দু যৌথভাবেই পালন করে। বৈশাখী মেলাও তাই। মেলায় হিন্দুরা যেমন দোকান দেয়, তেমনি দেয় মুসলমানরাও। মেলায় যেমন হিন্দুরা যায়, তেমনি যায় মুসলমানরাও। মঙ্গল শোভাযাত্রায় হিন্দুরা যেমন অংশ নেয়, তেমনি অংশ নেয় মুসলমানরাও। নাগরদোলা, পুতুলনাচ, বলিখেলা, ঘোড়াদৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, গম্ভীরা, বায়স্কোপ, বাঁদরনাচ, কবিগান, যাত্রাপালা, ধামের গান, শরীয়তি, মারেফতি, ভাওয়াইয়া ও পল্লীগান...এগুলোর কোনোটাই একতরফা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নয়, এগুলো সমগ্র বাঙালির। এসবের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে জাতীয়তার। এগুলো বাঙালির উৎসব।
একটি পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী প্রশ্ন তোলে, মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ভাল্লুক-পেঁচা প্রভৃতি প্রাণীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়। প্রতিকৃতি তৈরি বা অঙ্কন যেহেতু ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেহেতু মঙ্গল শোভাযাত্রাও সাংঘর্ষিক। যারা এসব কথা বলেন তারা অজ্ঞতাবশত বলেন। বর্তমান কালে এসব কথা বলা খুবই হাস্যকর। ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তো অনেক কিছুই আছে, যা আপনি প্রতিনিয়তই করে যাচ্ছেন। আপনি পকেটে যে টাকা নিয়ে নামাজ পড়েন সেই টাকার গায়ে মানুষ ও প্রাণীর প্রতিকৃতি আছে। বিদেশ ভ্রমণসহ নানা কাজে আপনাকে অবশ্যই ছবি তুলতে হয়। আপনি টিভি দেখছেন, টিভিতেও দেখা যাচ্ছে মানুষ ও পশুপাখির প্রতিকৃতি। আপনি ফেসবুক ব্যবহার করছেন, সেখানে তো প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ আর পশুপাখির প্রতিকৃতি ভেসে উঠছে। এসব প্রতিকৃতির সঙ্গে মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাঁশ আর কাগজের তৈরি ওসব প্রতিকৃতির ফারাকটা কোথায়? আপনারা মূর্তি বলতে যা বোঝেন, এসব প্রাণীর প্রতিকৃতি তা নয়। পূজার উদ্দেশ্যে যদি প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়, তবেই তা আপনার ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। মঙ্গল শোভাযাত্রায় এসব প্রাণীর ছবি পূজার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় না, তৈরি হয় শুভ-অশুভের প্রতীক হিসেবে। এসব প্রাণীর সঙ্গে রয়েছে বাঙালির হাজার বছরের শুভ ও অশুভের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের কথা লিখতে হলে আস্ত একটা বই হয়ে যাবে।
আর এসব প্রতিকৃতি শুধু বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হয় না, পৃথিবীর বড় বড় মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতেও প্রদর্শিত হয়। ভাস্কর্যও কিন্তু এক ধরনের প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতি রয়েছে ইসলামের আবির্ভাবের দেশ সৌদি আরবেও। জেদ্দার হামরায় রয়েছে উটের দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য। সেদেশে খেলনা পুতুল বিক্রি হয় বৈধভাবেই, যা খুবই জনপ্রিয়। শুধু সৌদি আরবে নয়, ইরান, ইরাক, মিশর, সিরিয়াসহ অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই ভাস্কর্য রয়েছে। ইরান, মিসর, ইরাকের জাদুঘরে রয়েছে অসংখ্য ভাস্কর্য এবং প্রাচীন শাসক ও দেব-দেবীর মূর্তি। এসব দেশে উন্মুক্ত স্থানেও রয়েছে অনেক ভাস্কর্য। ইরানে আছে একটি বিশাল স্বাধীনতাস্তম্ভ, যার নাম ‘আজাদী’। স্থাপত্যটির ডিজাইনার হোসেন আমানত একজন মুসলমান। কবি ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, পারস্যের নেপোলিয়ন বলে খ্যাত নাদির শাহ’র মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ভাস্কর্যও রয়েছে ইরানে। মাশহাদ নগরীতে ভাস্কর্যসংবলিত নাদির শাহ’র সমাধিসৌধটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। রাজধানী তেহরানে দু’বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয় সমকালীন ভাস্কর্য প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। ইরানের মাজানদারান প্রদেশে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় বালির তৈরি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর। এটি একটি উৎসব, যার নাম ‘স্যান্ড স্কাল্পচার ফেস্টিভ্যাল’। বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর মাজারের সামনেই তাঁর একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে।
মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইরাকেও আছে অনেক ভাস্কর্য। বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে ডানার ভাস্কর্যটি দৃষ্টিনন্দন। আল-মনসুর শহরে মনসুরের একটি বিশাল ভাস্কর্যসহ অনেক সাধারণ সৈনিকের ভাস্কর্য আছে। বাগদাদের আল-ফেরদৌস স্কয়ারে গড়ে তোলা হয়েছে মা-বাবা ও সন্তানের তেইশ ফুট উঁচু এক চমৎকার ভাস্কর্য। এটি তৈরি করেছেন তরুণ ইরাকি ভাস্কর বাসিম হামাদ আল-দাবিরি। মুসলমানদের কাছে মক্কা ও মদিনার পর সবচেয়ে পবিত্র নগরী বাগদাদ। এই নগরীতে আছে বাদশাহ শাহরিয়ার ও বেগম শাহেরজাদ, কাহরামানা, ডানাসহ আরো অনেক ভাস্কর্য।
পিরামিডের জন্য মিশরের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। বিরাটত্বের দিক থেকে বিখ্যাত হলো জোসার বা স্টেপ (সোপান) পিরামিড ও গিজা পিরামিড। পাথরের তৈরি স্ফিংসের মূর্তিসংবলিত গিজা পিরামিড সারা পৃথিবীর পর্যটকদের অতি প্রিয়। খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দের এসব মূর্তি মিশরের মুসলমানরা ধ্বংস করে নি, বরং রক্ষা করেছে গৌরবের সঙ্গে।
তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে ইবনে সিনার একটি বিশাল ভাস্কর্য আছে। সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাবেসি দ্বীপের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত শহর মানাদোতে রয়েছে যিশু খ্রিষ্টের এমন একটি ভাস্কর্য, যেটি এশিয়ায় সবচেয়ে উঁচু। বত্রিশ মিটার উঁচু একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তিরিশ মিটার উঁচু ভাস্কর্যটি। ইন্দোনেশিয়ার বালিসহ নানা প্রদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কতো দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে, সেদেশে না গেলে তা বিশ্বাস করানো যাবে না।
আগেই বলেছি, ভাস্কর্যও এক ধরনের প্রতিকৃতি। পৃথিবীর বড় বড় মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে যদি ভাস্কর্য থাকতে পারে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রাণীদের প্রতিকৃতি থাকলে অসুবিধা কোথায়? মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরুদ্ধাচরণ বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র বলেই মনে করি।
অপরদিকে, কালের বিবর্তনে বর্ষবরণের উৎসবে যোগ হয়েছে নানা মাত্রা। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এখন দেশের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজপোর্টাল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। পোশাক কোম্পানিগুলো নববর্ষ উপলক্ষে বাজারে আনে নানা ধরনের বাহারি পোশাক। সরকারি চাকরিজীবীদের দেয়া হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বোনাস। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরে দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী মেলা। কেউ কেউ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরের সমালোচনা করেন। এ নিয়ে তাদের হাহাকারের সীমা নেই। কেন হাহাকার? এতে কি বাঙালি সংস্কৃতির কোনো অঙ্গহানি ঘটে? মোটেই না। সংস্কৃতি কোনো স্থির-নিশ্চল বিষয় নয়। সংস্কৃতি নদীর মতো প্রবাহমান। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি অগ্রসর হয়। যে যার মতো করে নববর্ষ উৎসব পালন করুক, স্পন্সর করুক, তাতে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করি না। সবার সম্মিলিত উদ্যোগ, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ আরো বেশি সম্প্রসারিত হবে। এর সম্প্রসারণ দরকার। কারণ বাংলাদেশে বাস করে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা আলাদা উৎসব। নেই কোনো সার্বজনীন উৎসব, যেখানে মিলিত হবে সব সম্প্রদায়ের মানুষ। নববর্ষই একমাত্র উৎসব, যেখানে অংশ নেয় সব সম্প্রদায়ের মানুষ। এটিই বাঙালির সত্যিকারের সার্বজনীন উৎসব। এই উৎসবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত। ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। আত্মপরিচয়ের জন্যই বাঙালিকে ধরে রাখতে হবে এই উৎসব। এবং আমরা তা ধরে রাখবোই।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/১৬ এপ্রিল ২০১৯/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন